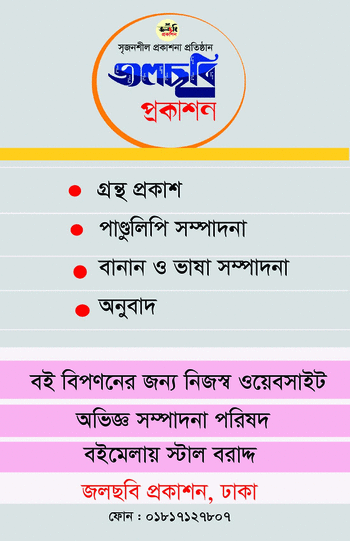পুরানো সেই দিনের কথা... [১]
নাসির আহমেদ কাবুল ।।
হঠাৎ একটি অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র পেলাম। ১৯৭২ সালের কথা। আমি তখন মঠবাড়িয়ায় কে এম লতিফ ইন্সস্টিটিউশনে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। সবে সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয়েছে আমার মেজো বোন দোদুলের সঙ্গে। দু-চারটি গানও শিখেছি হারমোনিয়ামের রিড টিপে। আমাদের সঙ্গীতের ওস্তাদে ছিলেন বাশিরাম শীল ও তবলায় ধলু দা। সদ্য স্বাধীন দেশ, শিল্প-সংস্কৃতিতে প্রচণ্ড সাড়া। স্বাধীন দেশে প্রথমবারের মতো নজরুল জয়ন্তী পালন করা হবে। আমরা অর্থাৎ আমার ইমিডিয়েট বড়ো বোন দোদুল, চাচাতো ভাই ও বন্ধু মিযানুর রহমান তসলিম ও তকদির এবং ডা. জাকির হোসেন মন্টু একই সঙ্গে মঠবাড়িয়ার ব্যাংকপাড়ায় বড়ো হয়েছি। বয়সে আমরা একে অপরের কাছাকাছি। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই নজরুল গীতি গাইতাম। তসলিম এখন বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী, মন্টু টেলিভিশন শিল্পী ও ডাক্তার। সরকারের প্রশাসন ক্যাডারে চাকরি করত। আমি মিডিয়ায় কাজ করেছি। তকদির তার ব্যবসা নিয়ে থাকে। এই লোকটি প্রচন্ডরকম সংস্কৃতি কর্মী। আমরা সবাই একই সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাই গাইতাম। পাড়ায় মনটুর বড়ো বোন রওশন আপা বেশ ভালো গাইতেন। তার ছোট বোন এমিলি (প্রয়াত) অনুষ্ঠানে নাচতো। এদেরকে নিয়ে মঠবাড়িয়া উদীচীর যাত্রা শুরু। শাখা গঠন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শংকার সাওজাল (শংকরদা)।
একদিন হঠাৎ করে অনুষ্ঠানে গান গাইবার একটি দাওয়াতপত্র পেলাম। খামের ওপর হাতে লেখা আমার নাম- ‘মাস্টার কাবুল’ । ১৯৭২—এর সে সময়ে আমি ক্লাস এইটের ছাত্র। ‘মাস্টার’ কথাটার অর্থ বুঝলাম না। খামটার ওপর বার বার চোখ বুলাতে লাগলাম। আবেগ—উত্তেজনায় আমি ঘেমে যাচ্ছিলাম। একটি অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার দাওয়াতপত্রটি আমার কাছে তখন অমূল্য সম্পদ বলেই মনে হয়েছিল। পরে অবশ্য জেনেছিলাম, ছোটদের নামের পূর্বে ‘মাস্টার’ আর বড়দের ক্ষেত্রে জনাব বা ‘মিস্টার’ লিখতে হয়। দাওয়াতপত্রটি আমাদের ব্যাংকপাড়ার বাসায় এসে আমার হাতে দিয়েছিলেন ডাক্তার নজরুল ইসলাম (তিনি তখন ছাত্রলীগ করেন)। পরে তিনি ঢাকা হৃদরোগ ইন্সস্টিটিউশনে অধ্যাপক হয়েছিলেন। আমার প্রয়াত বোন দোদুলও একই রকম চিঠি পেয়েছিল। নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে গান গাইবার চিঠি। দুর্ভাগ্য যে, সে বছর আমরা কমিউনিটি সেন্টারে ছোট পরিসরে অনুষ্ঠান করেছিলাম, আমাদের নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল জব্বার চাচা। তিনি মঠবাড়িয়ার সাংস্কৃতি পরিমণ্ডলের বিশিষ্টজন ও সংগঠক ছিলেন।
জীবনে সেই প্রথমবার কোন একটি অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলাম। গানটি ছিলো নজরুল গীতি। কথাগুলো মনে আছে ‘নিশি ভোর হলো জাগিয়া/পরান প্রিয়া...’। ওই বয়সে এত কঠিন একটি গান গাওয়া একেবারেই ঠিক হয়নি, পরে বুঝেছিলাম। কী গেয়েছিলাম সেদিন, জানি না। হঠাৎ হাততালিতে বাস্তবে ফিরে এলাম আমি। মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম, তাহলে ভুল কিছু গাইনি! তবে ভুল গেয়েছিলাম আমি, তাল কেটেছিল বেশ কয়েকবার।
এরপর থেকে স্থানীয়ভাবে আমি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়লাম। স্বাধীনতার পর প্রতিটি মানুষের চোখে নতুন স্বপ্ন, নতুন উদ্দীপনা। আমরাও গানের অনুষ্ঠান করছি, নাটক করছি। কিন্তু ওই সময়ের যেসব উদ্দীপনামূলক গান গাওয়া দরকার আমি সেগুলো জানতাম না। এ ক্ষেত্রে ধূমকেতুর মতো আবিভূর্ত হলেন শংকর সাঁওজাল, আমরা সবাই যাকে শংকর দা বলে ডাকি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই তিনি ভারত থেকে দেশে চলে আসেন। শংকর দা’র কণ্ঠের গণসঙ্গীত তখন মানুষকে পাগল করে ছাড়ছে আর কি। তার সঙ্গে ছিলেন বাসুদেব মিত্র। তিনি আমাদের এলাকার গানের শিক্ষক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। যদিও তার কাছে আমার গান শেখা হয়নি।
শংকর সাঁওজাল একজন নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, গণসঙ্গীত শিল্পী এবং চিত্রশিল্পীও। তার মতো একজন গুণী মানুষের সাহচর্য পাওয়া আমার জন্য খুব সৌভাগ্য বলেই মনে করি। তার নেতৃত্বে আমার নিজ থানা পিরোজপুর জেলায় মঠবাড়িয়ায় আমরা উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ও খেলাঘর আসর (খেয়া খেলাঘর)—এর শাখা গঠন করি। এই দু’টি সংগঠনের মাধ্যমে আমরা এলাকায় সাংস্কৃতিক জগতে একটি বিপ্লব এনেছিলাম। আমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানে মানুষের উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করতাম সে সময়ে।
অনুষ্ঠানগুলোতে তখন গণসঙ্গীত বলতে যা বোঝায় উদ্দীপনামূলক গান পরিবেশন করা হতো বেশি। থাকতো রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল গীতিও। সে সময় আমরা গাইতাম ‘জয় বাংলা বাংলার জয়’, পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল’, ছোটদের বড়দের সকলে’ —এ ধরনের গান। শংকর দা খুব দরদ দিয়ে গাইতেন ‘দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা/কারো দানে পাওয়া নয়’। সে সময়ে আমরা নতুন কিছু গানের অভাব অনুভব করলাম। এগিয়ে এলেন আলমগীর কবির আবু ভাই। তখন তিনি মঠবাড়িয়া কলেজের ছাত্র। পরে আবু ভাই বাংলাদেশ বেতারের মনোনীত গীতিকারের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ঝিনুক মালা ছবির জনপ্রিয় গানগুলো তারই লেখা। আবু ভাই গান লিখতে শুরু করলেন। তার লেখা গানে সুর করতে লাগলেন শংকর দা ও বাসু দা। চমৎকার সেসব গান আজও আমার মনে দাগ কেটে আছে। গানগুলোর মধ্যে একটি ছিল, ‘দেখো তোমার বাতায়নে/ ভোরের পাখি সূর্য এনে/ ভরিয়ে রেখেছে/ছড়িয়ে রেখেছে’। সুর করেছিলেন বাসু দা। খুব চমৎকার এই গানটি আমার সংগ্রহে নেই, এটা খুবই দুঃখজনক।
এই প্রসঙ্গে আরও কিছু নাম উচ্চারণ না করলেই নয়। আমি যার কাছে গান শিখতাম তিনি বাশীরাম শীল। বাজারে চুল কাটার কাজ করতেন তিনি। তার সঙ্গে তবলা বাজাতে আমাদের বাসায় আসতেন ধলু দা। সন্ধ্যা হলেই পড়াশুনা বাদ দিয়ে বাবার আগ্রহে আমার এক বোন দোদুল ও আমি গান শিখতাম। বাকিরা তখন ছোট। ওদের গান শেখার বয়স তখনও হয়ে উঠেনি। আমার মেজো বোন দোদুলের কিছু প্রিয় গান ছিল। তার মধ্যে ‘খেলো খেলো দ্বার/রাখিও না আর’, ‘শিউলি ফুলের মালা দোলে’, চেয়ো না সুনয়না, আর চেয়ো না/ এ নয়ন পানে’ গানগুলো আজও আমি খুব অন্তর দিয়ে একাকী গাই। আর চোখের সামনে ভেসে ওঠে দু’টি মুখ। একটি আমার মেজোবোন দোদুল, অন্যটি বাশীরাম শীল। দোদুল ক্লাস নাইনে পড়াকালীন নিউমোনিয়ায় মারা যায় ১৯৭৩ সালের ৫ আগস্ট, শনিবার।
২০০১ সালে ওর কবরের পাশে প্রথম গিয়েছিলাম। তার আগে গিয়েছিলাম আমার বাবার নতুন কবরটির পাশে। দোদুলের কবরের পাশে গিয়ে আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি। খুব কেঁদেছিলাম সেদিন। আর বাশীরাম শীল দা’ স্বাধীনতার পর ভারতে চলে যান। শুনেছিলাম, তিনি নাকি অন্ধ হয়ে গেছেন। খুব দেখার ইচ্ছে ছিল আমার। এ জীবনে হয়তো আর দেখা হলো না। জানি না তিনি বেেঁচ আছেন কিনা। আর ধলু দা! তিনি কেন যেন আমাকে খুব পছন্দ করতেন। আমার সঙ্গে তিনি তবলা বাজাতেন মনপ্রাণ দিয়ে। ২০০১ সালে একদিন গিয়ে ধলু দা’র পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। আমাকে চিনতে কষ্ট হলেও পরে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি।
শংকর দা’ দোদুলকে খুব মনে রেখেছেন। কতবার কতভাবে যে ওর নাম নিয়েছেন বলে বোঝানো যাবে না। একজন বড় মনের মানুষের এটিই মহত্ব, এই গুণটিই তাকে অনন্য করে রাখে।
আমিও একদিন একটি অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে আমার নিজের লেখা ও সুরে গান গাইলাম। শংকর দা যেন অভিভূত হলেন। তারপর সেই গানটির কথা কতবার যে আমাকে বলেছেন, কতভাবে উৎসাহ দিয়েছেন,তার হিসাব রাখা কঠিন।
কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে শংকর দা’ আমাকে সুযোগ দিতেন না। খুব রাগ করতাম। একবার উদীচীর হয়ে আবদুলাহ আল মামুনের লেখা ‘এখন দুঃসময়’ নাটকটি মঞ্চস্থ করতে গিয়ে আমি নাছোরবান্দা— আমাকে নাটকে পাঠ করতেই হবে। কিন্তু শংকর দা বঞ্চিত করলেন সেবারও। খুব রাগ করলাম— নাকি অভিমান জানি না। শংকর দা জানতে পেরে বললেন, ‘আরে বোকা তুই যদি নাটকে পাঠ করিস তো প্রোমট করবে কে? এই কাজ তো অন্য কাউকে দিয়ে হবে না।’ আমার দুঃখ কেটে গিয়েছিল। শংকর দা’র কণ্ঠে যাদু আছে মানুষকে বশ করার। সেটা তিনি জানেন কিনা জানি না। আমরা যারা তার সাহচর্যে ছিলাম, তারা বেশ ভালো করেই জানি।
শংকর দা’র সঙ্গে তখনও আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেনি। তিনি বড় ভাইয়ের বন্ধু। বড় ভাইয়ের মতোই তাকে সম্মান করি। একদিন সন্ধ্যায় তিনি ভাইয়ার সাথে আমাদের বাসায় এলেন। হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইলেন ‘আমার সকল দুঃখের প্রদ্বীপ/জ্বেলে দিবস গেলে করবো নিবেদন’। শংকর দা’র কণ্ঠে এই গানটি শোনার পর আমি এই গানটি শেখার জন্য পাগল হয়ে গেলাম। যে করেই হোক গানটি শিখতে হবে। শিখেছিলাম। এখনও যতবার এই গানটি গাই শংকর দা’র মুখটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ওই গানটি শোনার পর আমি রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুরাগী হয়ে উঠি।
কয়েক বছর কেটে গেলো। আমিও বড় হলাম। স্কুল ছাড়িয়ে কলেজ জীবনে। ঢাকার তিতুমীর কলেজে পড়ি। কলেজ ছুটি হলেই বাড়িতে দৌড়ে যেতাম। তখন আমরা উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর হয়ে শংকর দা’র নেতৃত্বে কোরাস গান গাইছি। সবগুলোই ছিলো গণসঙ্গীত। যেমন ‘ডিম পাড়ে হাঁসে/খায় বাগডাসে’, ‘ও দুনিয়ার মজদুর ভাইসব’ ‘উইশ্যাল ওভার কাম সাম ডেস’ ইত্যাদি। শংকর দা স্টেজে এসব গানের নেতৃত্ব দিতেন। আমিও তখন স্বপ্ন দেখতাম শংকর দা’র মতো আমিও এমন করে অনুষ্ঠান করবো। সে স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল আমার। শংকর দা একপর্যায়ে ঢাকা চলে এলে তার স্থানটি আমি নিয়েছিলাম। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কোরাস গানের নেতৃত্ব তখন আমিই দিতাম।
জীবনে অনেক মানুষের মধ্যে শংকর দা’র আমার কাছে অন্যরকম একজন মানুষ। ঢাকায় শংকর দা’র বেকার জীবনে বিয়ে করেছিলেন। পুরানা পল্টনের একটি বাড়িতে থাকতেন ভাবীকে নিয়ে। প্রতিদিন আমি যেতাম সেখানে। আমিও বেকার তখন। দু’তিনজনের ভাত আমরা চার—পাঁচজনে ভাগ করে খেতাম। চা খেতে চাইলে ভাবী বলতেন, ‘চিনি নাই। চিনি নিয়ে এসো।’ আমার এক বন্ধু ফিরোজ তখন ছোট একটি চাকরি করে। ভাবীর কথা মতো আমরা দু’জনে দৌড়ে যেতাম দোকানে। চিনি নিয়ে এসে ভাবীকে দিতাম। মনে হতো যেন ভারতবর্ষ বিজয় করে ফেলেছি। সেই কঠিন দিনগুলোতে শংকর দ’ার সঙ্গে রাস্তায় বের হলেই শংকর দা চা খাওয়াতেন। একদিন তিনি সরাসরি আমাকে সিগারেট অফার করে অবাক করে দিলেন। আমি খুব সংকুচিত ও কুণ্ঠিত হলাম। শংকর দা বললেন, ‘খাচ্ছিস তো, চুরি করে না খেয়ে সামনেই খেতে পারো। বড় হয়েছিস, লজ্জা কিসে!’ কথাগুলো আজও আমার কানে বাজে।
চলবে...

.jpeg)
.jpeg.jpg)
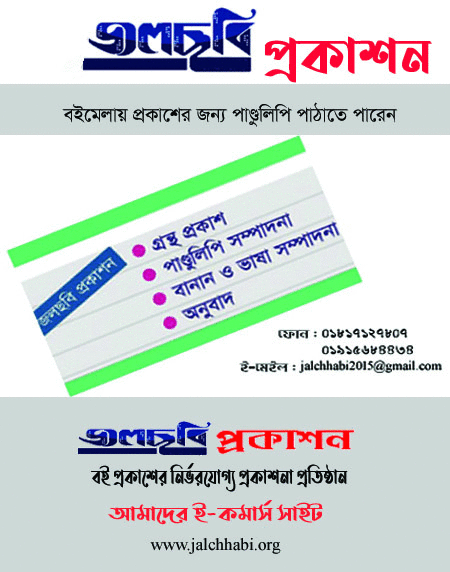


.jpg)